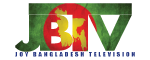নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন নির্ধারিত ৩ জানুয়ারির মধ্যে তাদের প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা দিতে শেষ পর্যায়ের কাজ করছে। নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার নিয়ে কথা বলেছেন কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার।
নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন জমা দেওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। মোটাদাগে আপনাদের সংস্কার প্রস্তাবের লক্ষ্য কী থাকবে?
আমাদের সংস্কারের লক্ষ্য থাকবে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা। আমাদের পুরোনো নির্বাচনী ব্যবস্থা ভেঙে গেছে, নির্বাচন নির্বাসনে চলে গেছে। এর থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে আইনকানুন, বিধিবিধান, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া—এগুলো কার্যকর করা এবং কতগুলো বিষয়ে আমাদের মধ্যে ঐকমত্য সৃষ্টি করতে হবে। কতগুলো বিষয়ে আমরা কোনোভাবেই আইনকানুন, বিধিবিধান দিয়ে পরিবর্তন করতে পারব না। কিছু জিনিস আছে অদৃশ্য। যেমন মনোনয়ন–বাণিজ্য। এটা হয় সংস্কৃতির কারণে। রাজনীতিতে ব্যবসায়ীকরণ হয়েছে। এই জিনিসগুলো আইন করে রোধ করা যাবে না। এর পরিবর্তনের জন্য রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন করতে হবে। এ জন্য একটি ঐকমত্য সৃষ্টি করতে হবে।
নির্বাচনব্যবস্থায় বড় ধরনের মৌলিক কোনো পরিবর্তন কি আসতে যাচ্ছে?
একটা মৌলিক বিষয় আলোচনায় এসেছে। নির্বাচনের বিদ্যমান পদ্ধতি থাকবে নাকি আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে, জনগণের মধ্যে বিতর্ক আছে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির পক্ষে থাকলেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাঁরা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পক্ষে নন। কারণ, এর মাধ্যমে স্বৈরাচারী যে দল বিদায় নিয়েছে তাদের একটা উপস্থিতি, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব থাকার সম্ভাবনা থাকবে। এটা একটা বড় বিতর্কের বিষয়। হ্যাঁ, আমরাও এটা নিয়ে আলাপ–আলোচনা করেছি; কিন্তু এই সিদ্ধান্তের এখতিয়ার সংবিধান সংস্কার কমিশনের।
এটা সংবিধানের বিষয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আপনাদের কমিশনের সুপারিশ কী থাকছে?
এখানে আমাদের কোনো সুপারিশ থাকছে না। এটা ওনাদেরই (সংবিধান সংস্কার কমিশন) সিদ্ধান্ত; তারাই সিদ্ধান্তটা নেবেন।
ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই অনেক সুপারিশ আপনারা চূড়ান্ত করেছেন। আপনাদের সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করতে কত সময় লাগতে পারে?
দুই ধরনের সুপারিশ আছে। কতগুলো এখনই বাস্তবায়ন করা সম্ভব। একটা এক অর্থে বাস্তবায়িত হয়ে গেছে, নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। আরও কতগুলো আশু প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে করা যায়। অনেকগুলো মনমানসিকতার পরিবর্তন আনতে হবে। কিছু আইন সংশোধন করে বা নতুন আইন করে বাস্তবায়ন করতে পারি।
তবে কতগুলো বিষয় এভাবে করা যাবে না। সংবিধান এভাবে সংশোধন করা যাবে না। আমাদের আকাঙ্ক্ষা হলো, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যেন ঐকমত্য হয়। রাজনীতিবিদেরা বলছেন, যৌক্তিক সংস্কারগুলো করা। কতগুলো যৌক্তিক সংস্কার কিন্তু এখন করা যাবে না। কিছু বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোরও দাবি আছে—যেমন দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ, সরাসরি ভোটে নারী প্রতিনিধিত্ব। আমি জানি না এগুলো নিয়ে এখনই কোনো পথ বের করা যাবে কি না। যদি বের না করা যায়, তাহলে আমরা আশা করব, এগুলোর ব্যাপারে একটা ঐকমত্য সৃষ্টি করে একটা জাতীয় সনদ প্রণীত হবে। সকল অংশীজন তাতে স্বাক্ষর করবে এবং পরবর্তী সময়ে বাস্তবায়ন করবে, এটা যেন সবার অঙ্গীকার থাকে। এটা যেন সবার নির্বাচনী ইশতেহারের অংশ হয়।
ন্যূনতম মানে কী, এটা অজানা। এর সংজ্ঞা কী?
আপনার কাছে এক রকম সংজ্ঞা হতে পারে, আমার কাছে আরেক রকম হতে পারে। আমি বলব, যেগুলো বাস্তবায়নযোগ্য এবং বাস্তবায়ন করা জরুরি, সেগুলো বাস্তবায়ন করা দরকার। আর যেগুলো এখন বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, সেগুলো পরবর্তী সময়ে ঐকমত্য সৃষ্টি করে বাস্তবায়ন করতে হবে। আমি মনে করি, যত বেশি বাস্তবায়িত হয়, এটা সবার জন্য ইতিবাচক। রাজনৈতিক দলের জন্যও ইতিবাচক। কারণ, রাজনীতিতে অনেক পক্ষ–বিপক্ষ থাকে। রাজনৈতিক দলের পক্ষে অনেক সময় অনেক কিছু করা দুরূহ। আমার মনে হয়, ঐকমত্য সৃষ্টি হওয়াটা নির্বাচনের আগেই সহজ।
ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই অনেক সুপারিশ আপনারা চূড়ান্ত করেছেন। আপনাদের সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করতে কত সময় লাগতে পারে?
নির্ভয়ে, বিনা দ্বিধায় কোনো রকম প্রভাবিত না হয়ে সবাই ভোট দিতে পারা। আর নির্বাচন এক দিনের বিষয় নয়। এটি একটি প্রক্রিয়া। এটা শুরু হয় ভোটার তালিকা থেকে। ভোটার তালিকা সঠিক হতে হবে। নির্বাচনে যাঁরা প্রার্থী হতে চান, তাঁরা যেন প্রার্থী হতে পারেন। আইনগত বাধা থাকলে সেটা ভিন্ন, এর বাইরে যেন কোনো বাধা না থাকে। যাঁরা প্রার্থী হবেন, তাঁদের সম্পর্কে যেন সবাই জানার সুযোগ পায়। প্রার্থীরা বাধাবিপত্তি ছাড়া প্রচার করতে পারবেন, টাকার প্রভাব থাকবে না। গণমাধ্যম নির্বিঘ্নে দায়িত্ব পালন করতে পারবে। নির্বাচন কমিশন নির্ভয়ে স্বাধীনভাবে জনগণের কল্যাণে নির্বাচনব্যবস্থাকে কার্যকর করতে কাজ করতে পারবে। ভোট গণনা হবে স্বচ্ছভাবে। কেউ অন্যায় করে পার পাবে না। পুরো প্রক্রিয়া হবে স্বচ্ছ ও কারচুপিমুক্ত।
এই প্রক্রিয়াটা স্বচ্ছ করার জন্য অনেকগুলো পরিবর্তন আনতে হবে। আইনে, প্রক্রিয়ায়, প্রতিষ্ঠানে, দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনতে হবে। এই প্রক্রিয়াটা সঠিক করার জন্যই সংস্কার। সংস্কারের জন্য প্রয়োজন ঐকমত্য। নিবাচন সুষ্ঠু করার জন্য সংস্কার দরকার। আর সংস্কারের জন্য ঐকমত্য দরকার। এগুলো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি আরেকটির বিকল্প নয়। নির্বাচন বনাম সংস্কার নয়, নির্বাচন এবং সংস্কার দুটোই দরকার।
বিএনপি বলছে, ন্যূনতম কিছু সংস্কার করে দ্রুত একটা নির্বাচন দেওয়া উচিত। আবার ছাত্ররা বা অনেকে বলছেন, এত মানুষের আত্মত্যাগ শুধু একটি নির্বাচনের জন্য নয় ।
এটার পক্ষে জোরালো যুক্তি আছে। এমন দাবিও এসেছে, ভবিষ্যতে যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে, তখনো যেন জাতীয় এবং স্থানীয় নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হয়। আমরা বিবেচনায় নিচ্ছি। স্থানীয় নির্বাচন আগে হলে অপেক্ষাকৃত ভালো লোকেরা নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ বেশি থাকবে। বর্তমান নির্বাচন কমিশনের নির্বাচন করার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। স্থানীয় সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে তারা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। আমাদের পুরো নির্বাচনী ব্যবস্থা ভেঙে গেছে, প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে গেছে। এগুলোর কার্যকারিতা দেখা যাবে। এ রকম যুক্তি আছে। আমরা এগুলো বিবেচনায় নিচ্ছি।
যাঁরা কোনো দলের প্রার্থী হবেন, তাঁদের ওই দলে ন্যূনতম তিন বছর সদস্য হিসেবে থাকতে হবে—এমন বিধানের কথা কেউ কেউ বলছেন। আপনারা এ বিষয়ে কিছু ভাবছেন কি না?
এ ধরনের প্রস্তাব আছে। এগুলোর পক্ষে জোর দাবি আছে। আমরা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছি। এ ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তাদের অবসর বা ইস্তফা দেওয়ার কত দিন পর নির্বাচন করতে পারবেন, এটা নিয়েও পক্ষে–বিপক্ষে দাবি আছে। এ ব্যাপারে আদালতেরও সিদ্ধান্ত আছে। এগুলো আমরা বিবেচনা করছি।
এখন আমাদের ভোটার হওয়ার বয়স ১৮। এটি ১৭ বছর হওয়া উচিত বলে উল্লেখ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। ভোটার হওয়ার বয়স কমানোর বিষয়ে অংশীজনদের কাছ থেকে আপনারা কোনো প্রস্তাব পেয়েছেন?
হ্যাঁ। ভোটার হওয়ার ক্ষেত্রে বয়স কমানোর প্রস্তাব এসেছে। তবে এটার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের সংবিধান সংস্কার কমিশনের।
বিদ্যমান ভোটার তালিকায় কি কোনো সমস্যা দেখছেন?
আমাদের এই ভোটার তালিকায় কিছু অসংগতি আছে। একটা হলো জেন্ডার গ্যাপ। নারী ভোটারের সংখ্যা কমে গেছে। ২০০৮ সাল নারী ভোটার ছিল মোট ভোটারের ৫০ দশমিক ৮৮ শতাংশ। তখন পুরুষের চেয়ে নারী ভোটার বেশি ছিল। কিন্তু এখন নারীর চেয়ে পুরুষ ভোটার বেশি। বাস্তবে আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি নারী। নারীরা ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হওয়া আমাদের ব্যর্থতা। নারীদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
আরেকটা হলো প্রবাসী ভোটার। দেড় থেকে দুই কোটি বাংলাদেশি প্রবাসে আছেন। তাঁরা আমাদের নাগরিক। তাঁদের ভোটের অধিকার আছে। কিন্তু প্রবাসীদের ভোটাধিকার সহজ নয়। এটার একটা প্রক্রিয়া হলো পোস্টাল ব্যালট। এটার সমস্যা হলো স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা কঠিন। কোনো কোনো দেশে এটা হয়তো করতে দেবে না। তার বিকল্প হলো ইলেকট্রনিক ভোটিং। এটার সমস্যা হলো আস্থার সংকট। এই জনগোষ্ঠীর ভোটাধিকার নিশ্চিত করা না গেলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রুটি পুরোপুরিভাবে দূর হবে না। তাই আমাদের অন্তত শুরু করা দরকার।
আপনারা গত তিনটি নির্বাচন পর্যালোচনার কথাও বলেছেন। কেন খারাপ নির্বাচন হলো—আপনারা কী খুঁজে পেয়েছেন?
এখনো আমরা এটা পর্যালোচনা করছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে বহু লিখেছি, কোন নির্বাচনে কী কী কারচুপি হয়েছে, এগুলো চিহ্নিত করেছি। এখন আমরা নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনে যাঁরা যুক্ত ছিলেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, প্রশাসনের কর্মকর্তা, প্রিসাইডিং কর্মকর্তা, পোলিং কর্মকর্তা, পর্যবেক্ষক, গণমাধ্যম সব স্তরের ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। এর থেকে আরও বোঝার চেষ্টা করেছি। যাঁরা নির্বাচনী কাজে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে একটা বড় জিনিস এসেছে, তাঁরা বলেছেন অনেক অর্থনৈতিক লেনদেন হয়েছে। এগুলো আমরা জানতাম। এখন সত্যতা নিশ্চিত হয়েছে।
আপনারা নির্বাচন কমিশনকে দায়বদ্ধ করার একটি জায়গা তৈরির কথা ভাবছেন। আবার কেউ কেউ বলছেন, এটি করতে গেলে নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা খর্ব হতে পারে।
এখন একটা দায়বদ্ধতার কাঠামো আছে। কিন্তু সেটা কার্যকর নয়। যেমন—আমরা নূরুল হুদা কমিশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন করে দায়বদ্ধতার মধ্যে আনার দাবি করেছিলাম। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রপতি এ বিষয়ে কর্ণপাতও করেননি। আরপিওতে ৭৩-৯০ ধারা পর্যন্ত নির্বাচনী অপরাধের কথা বলা আছে। কিন্তু কারও শাস্তি হয়েছে জানা নেই।
এখানে সবচেয়ে বড় অংশীজন হলো নির্বাচন কমিশন। তারা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। তারা সংবিধান সমুন্নত রাখার শপথ করেছিল। তার মানে গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখতে তারা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন করার শপথ নিয়েছে। কিন্তু তারা সে দায়িত্ব পালন করেনি। সংবিধানের শপথ ভঙ্গ করেছে। তাদের দায়বদ্ধ করা দরকার। আমরা দায়বদ্ধতার কথা বলছি, নির্বাচন কমিশনের কাজে বাধা দিতে নয় বা স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য নয়। যে বিষয় বিবেচনায় নিচ্ছি তা হলো—তারা যেন অন্যায় করে পার পেয়ে না যায়। এমন একটা কাঠামো থাকতে হবে, যাতে তাদেরও দায়বদ্ধ করা যায়।
আপনাদের সংস্কার প্রস্তাব বা প্রতিবেদন কি প্রকাশ করা হবে?
আমরা জানি না। এটা সরকারের মালিকানা। সরকারের সিদ্ধান্ত দিতে হবে। আমার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা হলো এটা প্রকাশ করা উচিত। এটা প্রকাশ করলে এর ভিত্তিতে একটা ঐক্য গড়ে উঠতে পারে। কমিশনগুলোর সব প্রস্তাব সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এগুলো প্রকাশ করা হলে একটা জনদাবি উঠতে পারে। এগুলো প্রকাশ করলে জনগণ মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পাবে। এটা ইতিবাচক হবে।